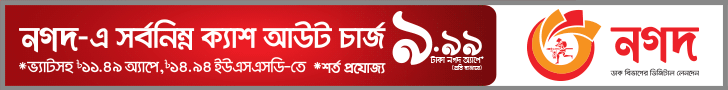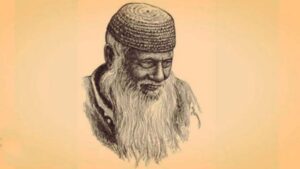
সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চিরকালের লড়াকু নায়ক মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র জাতীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক বিপ্লব, তথা পরিবর্তনের কথা ভাবতেন। মওলানা বিশ্বাস করতেন, এই ঘুণেধরা সমাজ বদলানোর জন্য দরকার ব্যাপক গভীর সাংস্কৃতিক বিপ্লব। নিজ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে দরকার নিজস্ব সংস্কৃতির নিরলস চর্চা, বিকাশ ও সম্প্রসারণ। নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে তিনি বুঝতেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি, মাটির সংস্কৃতি। কৃত্রিমতার বাইরে যে আবহমান বাংলাদেশ তার অন্তরঙ্গ ও বহিরাঙ্গে প্রাণপঙ্কের মতো মিশে যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি।
ষাটের দশকে চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লব তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল নিজ দেশের কায়েমি স্বার্থের অচলায়তনের ভিত বিনষ্টে এগিয়ে যেতে। তার কাছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রতিভাত হয়েছিল বড় ধরনের হাতিয়ার হিসাবে :
‘আর এই বিপ্লব মানুষকে লইয়া মানুষের জন্যই অনুষ্ঠিত হইবে।’
সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে জরুরি কথা নিবন্ধে তিনি লেখেন:
‘যে মানুষের জন্য এই বিপ্লব করা হয়, তাহারা কে?’
নিজেই উত্তর দিয়েছেন :
‘তাহারা হইতেছে দেশের জনসাধারণ, যাহারা সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষিত ও নিগৃহীত হইতেছে। এই শোষণের অবসান ঘটাইয়া সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থা কায়েম করিবার প্রাথমিক স্তর হিসাবে দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন।’
দেখা যাচ্ছে, মওলানা ভাসানীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল কথা সব ধরনের শোষণ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা। সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়ে তোলা। এই কর্মকাণ্ড তার কাছে কখনো সামাজিক বিপ্লব, কখনো ইসলামি সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ফলে নাগরিক পরগাছা শ্রেণিভুক্ত বুদ্ধিজীবী এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে উদাসীন কেতাবি কমিউনিস্টরা অংশ নেয়নি এই প্রক্রিয়ায়। আর এ প্রক্রিয়ারই অংশ ছিল মওলানার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা, দর্শন, মহীপুরের ‘হক্কুল এবাদ মিশন’। গড়ে তোলেন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, চিত্তরঞ্জন একাডেমী, নজরুল সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র।
কেউ যদি এ কথা ভেবে বসেন বা চিন্তা করেন, সামাজিক বিপ্লবই মওলানার একমাত্র উদ্দীপনা সৃষ্টির কেন্দ্র, তাহলে ভুল হবে। কারণ সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার যে সংস্কৃতি, এ দর্শনে মওলানা তার আসামজীবন থেকেই কাজ করে গেছেন নিরলস। বিভাগ-পূর্বকালে তিনি যখন বাংলা-আসাম সাহিত্য সম্মেলন করেছিলেন, তখনো তা ছিল তার সাংস্কৃতিক দীক্ষারই একটা দিক। পরবর্তীকালে এ ধারা তিনি অব্যাহত রাখেন। আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সব ধারাই বারবার আন্দোলিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে তার দ্বারা। একদিকে তার প্রতিটি সভা-সেমিনার, সম্মেলনের অত্যাবশ্যকীয় অংশ ছিল মেহনতি জনগণের উপস্থাপিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা, অন্যদিকে প্রচলিত ধারার লেখক না হয়েও তিনিই হয়ে উঠলেন আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী ধারার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক এবং চালিকাশক্তি। অনুপ্রেরণার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমাদের দেশের সব কৃতী লেখক, কবি ও শিল্পী মওলানার অনুসারী হয়ে পড়েছেন।
মওলানার সাহিত্যপ্রেমও অতুলনীয়। দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছেন, ডেকেছেন, দেখেছেন অন্য অনেকের মতো বুদ্ধিজীবীদের, কবি-সাহিত্যিকদের, বিদেশি বার্ট্রান্ড রাসেল থেকে শুরু করে মাদাম রেম, পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমত, মনিকা ফিল্টন, মূলক রাজ আনন্দ, কাজী আবদুল ওদুদ, কুয়োমোজো, ইলিয়া ইরেন বুর্গ, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ূন কবির, মফিজ উদ্দিন হাজারিকা থেকে শুরু করে দেশের তরুণতম কবি-লেখকও বারবার ছুটে গেছেন তার সান্নিধ্যে। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ভাষা আন্দোলন, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বারবার তিনি টেনে নিয়ে গেছেন স্বজনের শ্যামল উঠানে। সেজন্য এ কথা খুব বেশি বলা হয় না, আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন যতবার আমরা পর্যালোচনা করব, ততবারই স্বভাবসুলভ উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত করবেন তিনি এ অঙ্গনকেও।
কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন তো বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির ধারা এবং ইতিহাসই পালটে দেয়। রাজনৈতিক সম্মেলনের পাশে এ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মওলানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সংগীত সম্রাট আব্বাস উদ্দীন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শিক্ষাচার্য ড. শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেনের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বরা। সারা দেশের কয়েকশ বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি এতে অংশ নেন। এ বুদ্ধিচর্চার পাশাপাশি আসন নিলেন আমাদের লোকসংস্কৃতির কৃতী পুরুষরা। রমেশ শীল থেকে শুরু করে অনেকেই ছিলেন এ কাতারে। পরিবেশিত হয় বাউল, জারি, সারি, যাত্রাপালা, লাঠিখেলা ইত্যাদি।
মওলানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা বৃদ্ধির জন্য সর্বস্তরের জনগণকে সামগ্রিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্য সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেবক, সেবিকা, কর্মী গড়ে তোলার দিকেও মনোযোগ দেন। মহীপুরের হক্কুল এবাদ মিশন থেকেই তাই তো শুরু করেন তার বিখ্যাত ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব’-এর কাজ। ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে জরুরি কথা’ নিবন্ধটিতে ধরে রেখেছেন তার এ ক্ষেত্রের চিন্তাধারা। এ নিবন্ধে দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীদের কর্মতৎপরতার ওপরই সাফল্য নির্ভর করছে-এ কথা বলছেন মওলানা। অর্থাৎ কোনো অবস্থায়ই ব্যর্থতার দায় জনগণের ওপর বর্তায় না। কর্মীদের ঔদ্ধত্য ও একগুঁয়েমি বিপ্লবের ব্যর্থতা ডেকে আনবে। মওলানা বিশ্বাস করেন :
‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক যুগান্তকারী নতুন জীবনের দিশারি কর্মপন্থা।’
মওলানা লেখেন :
‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করিবেন কাহারা? সাংস্কৃতিক বিপ্লব বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার প্রাথমিক দায়িত্ব কাহাদের? ইহার পরিচালনা এবং ইহাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার দায়িত্ব হইতেছে এই মহান বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাসেবিকা ও কর্মীবৃন্দের।’
মওলানা মনে করেন, অংশগ্রহণকারীদের কর্মতৎপরতার ওপর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছে। সুতরাং :
‘এই মহান বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব হবে একটি প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা কায়েমের পূর্বাভাস, তাহা জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিবার কঠিন দায়িত্ব বিপ্লবী কর্মীরা পালন করিবে।’
কর্মীদের কাজের ধরন কেমন হবে, পরিচালিত হবে কীভাবে, তা নিয়েও ভেবেছেন এই মহান মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক পুরুষ। এই প্রবন্ধেই তিনি লিখেছেন :
‘কর্মীরা নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণের জীবনের সাথে মিশিয়া তাহাদের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলিও তুলিয়া ধরিবে এবং উহা সমাধানের জন্য আন্দোলন করিবে। জনসাধারণের সাথে আলাপ-আলোচনা করিতে হইবে, তাহাদের কথা শুনিতে হইবে। এই ধরনের আলাপ-আলোচনা হইতেই কর্মীরা তাহাদের কাজের শক্তি পাইবে। মনে রাখিতে হইবে, জনসাধারণ তাহাদের সমস্যার কথা কর্মীদের চাইতে ভালোভাবে বুঝেন, কারণ তাহারাই এই সমস্যায় জর্জরিত। কর্মীরা যেন সব জান্তার ভাব লইয়া জনসাধারণের সাথে কথাবার্তা না বলে, তাহা হইলে কর্মীরা জনসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করিবে এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অপূরণীয় ক্ষতি করিবে। কর্মীরা বিনয়, সহানুভূতি ও ধৈর্যের সঙ্গে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনিয়া, পরে কী করণীয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। ঔদ্ধত্য ও একগুঁয়েমি বিপ্লবের ব্যর্থতা ডাকিয়া আনিবে।’
এই স্বাপ্নিক মহাপুরুষের ভাবনায় যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব, তা কোনো সংস্কারমূলক কাজ ছিল না। তিনি জানতেন, সমাজের শোষণব্যবস্থার কাঠামো অটুট রেখে কেবল বাইরের দিকটা সংস্কার করলে দেশের মুক্তি হবে না।
এজন্যই :
‘সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গতি প্রবাহিত হইবে।’
মজলুম জননেতার চিন্তাকাশের সবটুকুই জুড়ে ছিল দেশের কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষের মঙ্গল কথা। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মানচিত্র আঁকতে গিয়েও তিনি এ ব্যাপারে ছিলেন পূর্ণ সজাগ।
তিনি লেখেন :
‘স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের আর একটি বড় দায়িত্ব হইতেছে কৃষক জনসাধারণকে তাহার অধিকার সম্পর্কে আন্দোলনের মাধ্যমে ক্রমেই সচেতন করিয়া তোলা। দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণহীন, সম্পদময় সুখী জীবন কৃষকের এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্মগত অধিকার। এই অধিকার হইতে যাহারা তাহাদের বঞ্চিত রাখিতেছে, তাহারাই হইতেছে অত্যাচারী শোষক শ্রেণির লোক। ইহাদের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি লইয়া সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালু রাখিতে হইবে।’
তাঁর মতে :
‘দীর্ঘদিনের অভাব, দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনার ফলে কৃষক জনসাধারণ ক্ষেত্রবিশেষে তাহাদের অধিকার সম্পর্কে অবচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা একটি মারাত্মক অবস্থা। এই অবস্থার সুযোগে শোষক শ্রেণীগুলি নানারূপ ছোটখাটো সংস্কারমূলক ব্যবস্থার দ্বারা কৃষক আন্দোলনকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার চেষ্টা করিবে। কৃষক সাধারণকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সমাজতান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থাই কেবলমাত্র তাহাদের সকল দুঃখ-কষ্টের পূর্ণ অবসান ঘটাইবে আর কোনো ব্যবস্থাই কৃষক জীবনে উন্নয়ন ও প্রাচুর্যের ছোঁয়া আনিতে পারিবে না। সাংস্কৃতিক আন্দোলন জনজীবনে এক নতুন আশার সঞ্চার করিবে।’
মওলানার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল :
‘সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণহীন, মহান সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। এই লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চলিতে থাকবে।’
এই জন্যেই :
‘স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কোনো কারিগরি বিদ্যা, শিক্ষকতা, হাতের কাজ, যেমন কাঠমিস্ত্রির কাজ, লোহার কাজ, কামারের কাজ, নতুন ধরনের ঘর বাঁধার কাজ, রাস্তাঘাট নির্মাণের ও মেরামতের কাজ, টিউবওয়েল ও অন্যান্য মেশিনপত্র, যাহা গ্রামাঞ্চলে ব্যবহার করা হয়, তাহা মেরামত করার কাজ, মৎস্য চাষের কাজ, গ্রামের শিশু ও নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষাদানের কাজ, সেলাই, পশুপালন ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষার কাজ ইত্যাদি শিক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিবে।’
কারণ : ‘সত্যিকার কাজের লোককে জনসাধারণ ভালোবাসেন। বাকসর্বস্ব ব্যক্তি বিপ্লবের পিঠে বোঝা।’
কর্মীদের দায়িত্ব ও কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জরুরি কথায় তিনি বলেছেন :
‘কর্মীরা নিজেদের সংঘবদ্ধ করিবে। নিজেদের মধ্যে স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধানের উপায় ও সেই সম্পর্কে কর্মসূচি লইয়া আলাপ-আলোচনা করিবে। তারপর সাত দিনের একটি কর্মসূচি বা প্রোগ্রাম লইয়া ঐ প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত করার জন্য আগাইয়া যাইবে। সুবিধা অনুযায়ী তিন দিন, সাত দিন, দশ দিন, পনেরো দিন এইভাবে কর্মসূচি বা প্রোগ্রাম করা উচিত। সময় নির্দিষ্ট করিয়া প্রোগ্রাম করিলে ওই প্রোগ্রাম শেষ করিবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হইলে ভুলত্রুটি কোথায় ছিল, তাহা আলোচনার মাধ্যমে শুধরিয়া লওয়া যায়। অনির্দিষ্টকালের প্রোগ্রাম অনেক ক্ষেত্রে শেষ হয় না এবং উহার ফলে কর্মী ও জনমনে হতাশা দেখা দেয়।’
মওলানা মনে করতেন, কাজ ও কাজ সম্পাদন করার সময় আগেই নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত। তার মতে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে পারলে কৃষক ও কর্মী উভয়পক্ষই বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে উঠবে।
এই কর্মবীর মনে করেন, কোনো কর্মীই সত্যিকার কর্মী হতে পারে না, যতক্ষণ না সে জনসাধারণকে প্রকৃত সেবা করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে।
কোনো কাজ স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা ভালোভাবে না করতে পারলে সে বা তারা জনসাধারণের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে আর জনসেবক থাকে না। সুতরাং, হাতের কাজ ভালোভাবে করার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।
সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যে যোগ্য, দক্ষ, সৎ, বিনয়ী, কর্মঠ, ধৈর্যশীল, সচ্চরিত্র, নির্ভীক, বুদ্ধিমান ও সাহসী কর্মী দরকার, তা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। আর তাই তার সাংস্কৃতিক চিন্তার বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে কর্মী ও কর্মীদের করণীয় সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা।
তিনি বিশ্বাস করেন :
‘স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের আদর্শ কর্মী হইতে হইবে। আদর্শকর্মী তাহারাই-যাহারা জনসাধারণের বিশ্বাস, আস্থা ও সহানুভূতি অর্জন করে। জনসাধারণ দেখিতে চায়, কর্মীরা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করিতেছে। যে কর্মী তাহার কাজের মধ্যে জনহিতকর কাজের সত্যিকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে, সে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সবচাইতে বড় বন্ধু।’
মওলানা জানেন, ‘বিপ্লব বিপ্লব করে চিৎকার করলেই বিপ্লব হয় না। জনসাধারণকে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত করতে হবে।’
বিপ্লব চরিতার্থ করার জন্য মহান নেতা আহ্বান জানান, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, খাদ্য গ্রহণে, বিলাসিতা বর্জনের। ডাক দেন সহজ-সরল জীবনযাপনের। পিকেটিং করতে বলেন মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের স্থানগুলোতে, জুয়ার আড্ডাসহ অনৈতিক কাজের কেন্দ্রগুলোতে। চোরাচালানি, ঘুসখোর, দুর্নীতিবাজদের প্রতিহত করার চিন্তাও তার ছিল।
তার এ চিন্তাচেতনা বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ হিসাবে, একইসঙ্গে বাংলাদেশের ওপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য সত্তর দশকে গঠন করলেন ‘জোয়ান কর্মী শিবির’। সাংস্কৃতিক বিকৃতি ও পরাজয়ের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষকে হুঁশিয়ার ও সচেতন করে তোলাই হবে যাদের কাজ।
নিজে প্রচলিত অর্থে লেখক ছিলেন না। তবু লিখেছেন। লেখার মর্যাদা তার মতো করে খুব কম নেতাই লিখেছেন। ১০টির মতো গ্রন্থের তিনি জনক।
মওলানাকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস। অঙ্কিত হয়েছে মূল্যবান ছবি। অন্য কথায় আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্য পুরোপুরিই প্রায়, একটা সময় পর্যন্ত আবর্তিত হয়েছে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে অথবা তার আদর্শ নিয়ে। মওলানাকে নিয়ে রাজনৈতিক গ্রন্থাদির সংখ্যাও কম নয়। সর্বোপরি বিশাল গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে যে লাখ লাখ মানুষ বাস করেন, তারা মওলানাকে নিয়ে রচনা করেছেন কিংবদন্তি, অজস্র গান।
বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, বিশেষ করে লোকসংস্কৃতি বিকাশের ও সংরক্ষণের যে তাগিদ মওলানা অনুভব করতেন, তা আমাদের এক অনুপ্রেরণার উৎস। আবার একইসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক লেনদেনের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ আর সাংস্কৃতিক মানবমণ্ডলী গড়ে তোলাও ছিল তার আরেক স্বপ্ন।
১৯৭২ সালে মওলানা বলেন :
১. বাঙালি জাতির জাতীয় সাংস্কৃতিক বিকাশ ও মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। জাতীয় সংস্কৃতি যাতে গণমুখী হয়, তার ব্যবস্থা করা হবে। এ জাতীয় সংস্কৃতি বাংলার গোটা জনগণ, বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের সংঘাতময় জীবন ও নিরন্তর শ্রেণি-সংগ্রামের একটা সার্বিক প্রতিফলন হবে।
২. সামন্তবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং গণতান্ত্রিক চরিত্রের নতুন গণসংহতির বিকাশ এবং বিস্তারের জন্য আমাদের জনগণের সৃজনশীল প্রতিভাকে মুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনের কাজ রাষ্ট্র ও সরকার হাতে নেবে।
৩. জনগণের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির উন্মেষ সাধনে উৎসাহ দান ও বিকাশের জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা-(ক) জনগণের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি সাধনে সাহায্য করবে, (খ) বর্ণগত ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে জনগণকে সাহায্য করবে, (গ) সমগ্র দেশের জনসাধারণের সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্মিলিতভাবে অনুন্নত জনসমাজ-সমেত প্রত্যেকটি জনসমষ্টিকে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারার বিকাশ সাধনে সাহায্য করবে।’ [বাংলাদেশের রাজনীতি : প্রকৃতি ও প্রবণতা : ২১ দফা থেকে ৫ দফা, পৃষ্ঠা : ২৪৯-২৫০]
এরকম কথা আর কেউ বলেননি এ দেশে।
আবদুল হাই শিকদার : কবি; সম্পাদক, দৈনিক যুগান্তর